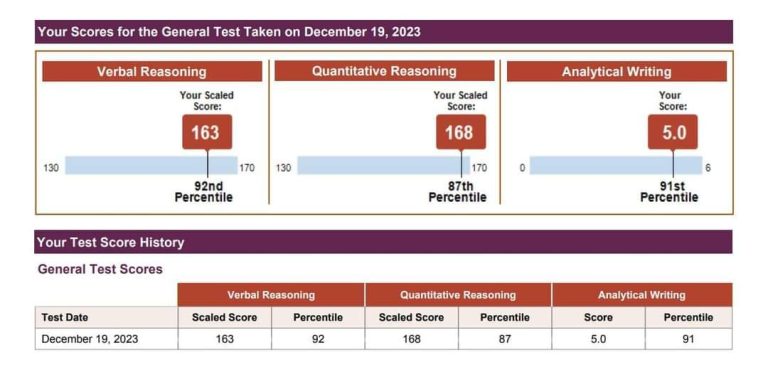Journal, Thesis Publication, Research paper
IoT and Machine Learning based ekti biomedical related thesis pape
Top contributor
Pipel Reja but ami honours ey research korar try krchi willingly MS abroad ey korar jonno.
Noor Bente Zakir It’s difficult for you, but not impossible. If you will manage a Professor of any university, who is also a researcher then you can.
মূল বিষয়টা বলি: গবেষণা শিখতে হলে থিসিস থাকতে হবে কোর্সে। ইডেনে বা ৭ কলেজে থিসিস নাই। আপনি অনার্স শেষ করে যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,জাহাঙ্গীরনগর, বুয়েটে মাস্টার্স ভর্তি এক্সাম দিয়ে ভর্তি হতে পারেন তাহলে আপনার মাস্ট থিসিস থাকবে। আর থিসিস করলেন মানেই গবেষণা বা গবেষণা কিভাবে করতে হয় সেটা শিখলেন।
অন্য সাবজেক্ট এ চাইলে করতে পারবেন।নিজের সাবজেক্ট এ পারবেন।
Research4life
হবু গবেষকদের জন্য! কিছু কমন কথা!!
তাহলে কি করনীয়?
আমি পাল্টা প্রশ্ন করেছি কি করতে বিদেশ বিভূঁইয়ে পাড়ি জমাবেন? উত্তর পড়াশোনা করতে।
তাহলে কি করণীয়?
বিঃদ্রঃ আমার মূল মেসেজ হলো আগে জানেন তারপর করেন।
অনার্স ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষের সময়ে কোন জবে (পার্ট টাইম) সাধারণত এগুলোর দরকার পড়েনা। তাই উপরে বর্ণিত ক ও খ এই তিন বছরে শিখে নিলে ফাইনাল পরীক্ষার পরে নিজেই লিখতে পারবেন। জানতে গিয়ে আপনি বেশ কিছু নিয়ম জেনে যাবেন। অর্থাৎ কিভাবে রেফারেন্স লিখতে হয়? অর্থাৎ APA, Vancouver, MLA, Chicago (২) সহ আরো অনেক পদ্ধতি।
পাদটীকাঃ
(১) গবেষণা কাজ সাধারণত কমই হয়। আগের বছরের গবেষণা কর্ম উত্তরাধিকার সূত্রে পায় কিংবা নীলক্ষেত থেকে সংগ্রহ করে নেয়।
(২) রেফারেন্স লেখার নিয়ম।
মাহাদী-উল-মোর্শেদ
পিএইচডি গবেষক
মনোবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
ও
হেড, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন, বন্ধু।
মেগা পোস্ট (আপডেটেড)
গবেষণা আর্টিকেল এবং থিসিস লেখার কিছু টুলস এবং সফটওয়্যার
আপনি থিসিস করেন কিংবা গবেষণা আর্টিকেল লিখেন,সাধারণত এই অংশগুলো থাকে-
• Title
• Abstract
• Introduction
• Literature Review
• Conceptual and Theoretical framework
• Methodology
• Results/Findings & Discussion
• Conclusion
• Reference
টাইটেল,অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথডোলজি, এবং কনক্লিউশন;এগুলো লেখার জন্য সাধারণত কোন সফটওয়্যার প্রয়োজন নেই। আপনার হাতে যদি সিমিলার কয়েকটি থিসিস/আর্টিকেল থাকে , তাহলে সে নমুনাগুলো অনুসরণ করলে খুব সহজেই এই অংশগুলো লিখে ফেলতে পারবেন । তবে এই অংশগুলোসহ গবেষণায় প্রত্যেকটি অংশে,কিছু টুলস এবং সফটওয়্যার প্রয়োজন হয়, Research Help Bangladesh এর ৬০ হাজার মেম্বার উপলক্ষে লিখছি-
1.Grammar checker-(Grammarly*/Ginger)
ইংরেজি যেহেতু আমাদের মাতৃভাষা না। তাই আমাদের লেখার মধ্যে ব্যাকরণগত এবং ভাষাগত অনেক ভুল থাকতে পারে । আপনি চাইলে সহজেই এখান থেকে ঠিক করে নিতে পারেন।সর্বোচ্চ আউটপুট পেতে চাইলে প্রিমিয়াম ভার্শন কিনতে পারেন। Grammarly অরিজিনাল অ্যাকাউন্ট প্রতিবছর ১৪ হাজার টাকার মতো লাগতে পারে। তবে মাঝে মাঝে ডিসকাউন্টে আরো কমে পাওয়া যায়।
2. Paraphrasing and writing tools-(Quillbot*/Word Ai/Ref-n-Write/Pro Writing Aid/Wordtune)
ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি Quilbot,Wordtune খুবই ভালো । তবে Pro Writing Aid খুবই অ্যাডভান্স। Quilbot এর বিনামূল্য ভার্শন আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করবে। অন্য টুলসগুলো আপনাকে নামমাত্র মূল্যে কিনে নিতে হবে ।সবগুলা টুলসের কম্পারিজন নিয়ে শীঘ্রই একটা ভিডিও বানিয়ে আপলোড দেওয়ার ইচ্ছা আছে।
3.Editing text software (Word*, OpenOffice, LaTeX*), Scrivener…)
মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর কাজ খুব ভালোমতো জানা থাকলে বাকি সফটওয়ারগুলো না শিখলেও হবে। তবে বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ল্যাটেক্স শেখা যেতে পারে।আমি গবেষণার দুটি সফটওয়্যার শিখে সবচেয়ে বেশি আনন্দলাভ করেছিলাম , তার মধ্যে একটি হলো লাটেক্স । জার্নাল অনুযায়ী লেখা সাজানো ,অটোমেটিক সূচিপত্র বানানো, ইত্যাদি সুবিধা পাওয়া যাবে।সুন্দর সুন্দর সিভি এর Latex Templete ও পাওয়া যায়। আমি Office 365 ব্যবহার করি । এখানে ভয়েস ইনপুট দেওয়ার সুবিধা আছে , ফলে আমাকে কষ্ট করে টাইপ করতে হয় না ।
4. Presentations (PowerPoint*, Prezi,Slidescarniva,Canva*)
Office 365 তে দারুন একটি সুবিধা আছে । সেটি হলো অনলাইন থেকে কোন একটি লেখা কে নিয়ে ,সেটিকে অটো পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড এ রূপান্তরিত করা যায় । Canva premium খুবই কম দামে পাওয়া যায় এবং দারুণ প্রেজেন্টেশন ভিডিও এর টেমপ্লেট পাওয়া যাবে। যারা বিভিন্ন কনফারেন্সে poster present করবেন ; এখান থেকে দারুন দারুন ইনফোগ্রাফিক পাবেন।
5.Conceptual and Theoretical framework(Diagram. net*,creatly*,Canva)
এই অংশগুলোতে অনেক সময় ডায়াগ্রাম বা চিত্র আঁকতে হয় । মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ডে যদিও চিত্র অঙ্কন করা যায় , তবে সেটি সুন্দর হয়না । আপনারা চাইলে Diagram. net,creatly,Canva এই ওয়েবসাইট গুলো থেকে মুহূর্তেই কাঙ্খিত ডায়াগ্রাম তৈরি করে নিতে পারবেন ।
6.Results/Findings & Discussion
এই অংশকে কোয়ালিটিভ এবং কোয়ান্টিটিভ দুটি ভাগে ভাগ করে বোঝালে সহজ হবে ।
• Quantative Analysis (SPSS*,Excel,Matlab,Python, STATA, R, …)
SPSS এর কাজ ভালোমতো জানলে সোশ্যাল সাইন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে শিক্ষার্থীদের বাকি সফটওয়ারগুলো না শিখলেও মোটামুটি চলে । R শিখতে পারেন , অ্যাডভান্স এনালাইসিস করতে পারবেন । পাশাপাশি খুব সুন্দর সুন্দর ফিগার বের করতে পারবেন।
• Qualitative research software (Atlas.ti,NVivo*,Quirkos,MAXQDA…Excel*)
এতগুলা সফটওয়্যার দেখে মোটেও ঘাবড়ে যাবেন না । গুণগত গবেষণা করার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সফটওয়্যার না হলেও চলে বা এক্সেল ব্যবহার করেই থিমেটিক এনালাইসিস করে ফেলা যায়। আমি এই দুটি সফট্ওয়ারে Quirkos,MAXQDA এর কথা বলবো । আপনারা চাইলে শিখে নিতে পারেন।
7.Questionnaire survey(Kobo toolbox*,Google form*)
Kobo toolbox খুবই স্মার্ট একটি টুলস । রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ পেতে হলে এই টুলস এর কাজ জানা আবশ্যক ।
8.Plagiarism Checker(Turnitin*, Viper,I-thenticate, Checker X)
DupliChecker,Paperrater,Plagiarisma,Search Engine Reports,PlagTracker,Plagium,CopyLeaks,Ephorus,Quetext অনেকেই এসব সোর্স থেকে প্লেজারিজম চেক করে তৃপ্তির ঢেকুর তোলেন । কিন্তু একাডেমিক লেখায় এই টুলসগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। অনলি Turnitin ইজ বস ।
9.Bibliography manager (Zotero*, Mendeley*,EndNote, …)
রেফারেন্সিং সফটওয়্যার ব্যবহার করে মুহূর্তের মধ্যেই রেফারেন্সিং করে ফেলা যায় । Zotero সফটওয়ারটি শেখা আমার জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে আমি মনে করি ।
গবেষণা প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেতে হলে এই সফটওয়্যার গুলো শেখা অত্যন্ত দরকার । Zotero এবং Mendeley আমি ব্যবহার করি। রেফারেন্সিং ছাড়াও বাড়তি কিছু কাজ করা যায়। আমি আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে নেওয়া ফ্রী ক্লাসে দেখিয়েছিলাম।
10.Some usefull tools and website
Researchgate,Google schoolar,Scihub,Scribbr,Researchrabbit,connectedpapers,Scilit ইত্যাদি নামগুলা লিখে গুগল সার্চ করলেই বুঝতে পারবেন যে, এগুলো কি কাজ।
মোরশেদ আলম
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
বাইরে পড়তে যেতে আপনাকে রিসার্চ এর বেসিক ও পেপার রাইটিং নিয়ে বিস্তারিত জানতে হবে। সাথে যদি কোনো পাবলিকেশন থাকে তা আপনার স্কলারশিপ প্রাপ্তিতে এক্সট্রা বেনেফিট দিবে।
রিসার্চ লার্নিং থেকে পেপার পাবলিকেশন পর্যন্ত সাপোর্টনিয়ে আপনার জন্য রয়েছে মাস্টারকোর্স। বিস্তারিত জানতে ভিজিট https://cutt.ly/RSRM
IP: 01
Research Tips: ইন্টারনেট ব্যবহার করে গবেষণায় কিভাবে Literature Search করবেন?
গবেষক যে বিষয়ে গবেষণা করবেন বলে মনস্থির করেছেন সে বিষয় বা শিরোনামকে কেন্দ্র করে তার ভূমিকা (Introduction) এবং সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review) লিখতে হয়। এখন কথা হলো কিভাবে আমরা খুঁজবো?
এখন গবেষক যে কাজ করবেন তা হলো Parental Acceptance-Rejection AND Aggression AND Adolescence এভাবে লিখে সার্চ দিলেই প্রত্যাশিত ফলাফল পেয়ে যাবেন। এভাবে অন্য
Truncation ব্যবহার করে অতিসহজেই এবং দ্রুত Literature Search করতে পারবেন।
একটা বিষয় মনে রাখতে হবে Literature সব সময়েই সাম্প্রতিক সময়ের হতে হবে। তাহলে সেটা কিভাবে খুঁজে বের করবো?
এভাবেই একজন গবেষক তার গবেষণায় অল্প সময় ব্যয় করে কাঙ্ক্ষিত Literature খুঁজে বের করতে পারবে।
মাহাদী-উল-মোর্শেদ
পিএইচডি রিসার্চ স্কোলার
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
রিসার্চ/থিসিস কি: কেন এবং কিভাবে করবেন এবং লিখবেন?
উচ্চ শিক্ষার (requirement) জন্য কিংবা গবেষক হতে চাওয়ার প্রথম ধাপ বলা চলে আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভ থেকে undergraduate/masters এর থিসিস। আমাদের অনেক প্রব্লেম থাকার পরও আমাদের এই ছোট দেশটিতে আমরা ম্যানেজ করে চলতে পারতেছি এটা অনেক বড় একটি পাওয়া। আর আমাদের প্রকৃতির সাথে তাল (দুর্যোগ) মিলিয়ে চলতে এবং অধিক মানুষের সঠিক খাদ্য ও বাসস্থান এর ব্যবস্থা করতে গবেষণার অধিক প্রয়োজন। কিনতু, সমস্যা হলো সঠিক guideline এর।
ভার্সিটি শেষ সময়ে থিসিস অথবা প্রজেক্ট নিতে হয়। এখন যারা একটু ভালো স্টুডেন্ট কিংবা Higher স্টাডির ইচ্ছা আছে অথবা টিচার হওয়ার ইচ্ছা তারা থিসিস বেছে নেয় । আর যাদের সিজিপিএ একটু কম থাকে কিংবা জবে ঢোকার তাগিদ থাকে তারা বেছে নেয় ইন্টার্ন অথবা প্রজেক্ট। কিনতু, যারা থিসিস নেয় তাদের উদ্দেশ্য মনে হয় খুব একটা ক্লিয়ার থাকে না। অনেকে বাজওয়ার্ড ভেবে নিয়ে নেয়, অনেকে higher স্টাডির জন্য নেয় !! কিনতু, তারা যা করে ৪/৮ মাসে তা কতটুকু প্রাসঙ্গিক তাদের higher স্টাডির জন্য এ বিষয়ে আমার এনাফ doubt আছে।
একজন প্রোফেসরের ল্যাবের ওয়েবসাইট তাঁর কাজকর্ম বোঝার জন্য সবচেয়ে ভালো জায়গা। এখানে তাঁর পাবলিকেশনগুলো সাজানো থাকে। বোঝা যায় তিনি রিসেন্ট বছরগুলোতে অ্যাক্টিভ কিনা। পাবলিকেশনগুলোর অনেকগুলো ডাউনলোডও করা যায়। তাঁর ল্যাবের গোল বা অবজেক্টিভ নিয়েও কথাবার্তা থাকে। ল্যাবে যারা কাজ করছে, তাদের প্রোফাইলও থাকে। কাজেই এটা দেখতে পারলে ভালো। এটাও বোঝার চেষ্টা করুন তাঁর ল্যাবে কী ধরণের কাজ হচ্ছে — অ্যানালিটিক্যাল, এক্সপেরিমেন্টাল, কম্পিউটেশনাল নাকি মিক্সড ধরণের। ভাবুন, আপনি এ ধরণের কাজের সাথে কম্ফোর্টেবল কিনা। কান্ট্রি, ইউনিভার্সিটি এবং নিজের এরিয়া নিয়ে একটা শর্ট লিস্ট করে রিসার্চ/ থিসিস এ যাওয়া দরকার।
[লেখার শুরুর আগে আমি একজনমানুষের নাম মেনসন করতে চাই ! Dr. Bulbul Ahmed (Researcher at Plant Biology Research Institute (Institut de recherche en biologie végétale, IRBV), U of Montreal) , স্যারের নিকট থেকে পাওয়া মোটিভেশন এবং সাপোর্ট এখন পর্যন্ত এতদূর নিয়ে এসেছে, মূলত রিসার্চ/ উচ্চ শিক্ষার স্বপ্ন স্যার কে দেখেই শিখেছি। ]
Process Map: Problem search → Research Question → Literature Review → Methdology → Results & Discussion → Conclusion (Depends on your work)
1. Problem Search:
সমস্যা অনেক ভাবেই খুঁজে পেতে পারেন। কিনতু যারা এই ফিল্ডে নতুন তাদের জন্য একটু কঠিনই বটে প্রব্লেম খুঁজে পাওয়া। আমি বলবো, যে ফিল্ডে কাজ করতে চান ঐ বিষয়ে প্রচুর আর্টিকেল (কনফারেন্স/জার্নাল) পড়ুন। এটা মূলত ট্রাডিশনাল ওয়ে , সহজে প্রব্লেম খুঁজে পাওয়ার। প্রথমে অনেক বড় প্রব্লেমকে আসতে আসতে break-down করে ফেলুন , তারপর সবচেয়ে narrow পার্ট নিয়ে আপনার কাজটি এগিয়ে নেন। আগে আপনার পছন্দের ডোমেইন এর জন্য কারেন্ট পেপারগুলো পড়ুন এবং সেগুলো থেকে শর্ট রিভিউ করে রাখুন (জার্নাল/ কনফারেন্স পেপার) .এটি সবচেয়ে কম সময়ে ভালো একটি সমস্যা খুঁজে পাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায়
#How to compress your idea/topic?
যেমন ধরুন আপনি বাংলাদেশের চর অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ডায়াবেটিসডিজিস নিয়ে একটি স্টাডি করবেন করবেন বলে স্থির করছেন । ডায়াবেটিস মেইনলি ৩ types। এক্ষেত্রে ভালো হবে একটি মাত্র টাইপ নিয়ে কাজ করা (such as type ২)। এবং আপনার টার্গেট পিপল গুলো শুধু ফিমেল অথবা প্রেগনেন্সি রিলেটেড হলে আপনার এরিয়া অনেকটায় সুনির্দিষ্ট হয়ে যাবে।
2. Literature Review
গবেষণা হয় মূলত তিন ধরণের: অরিজিনাল গবেষণা, রিভিউ বা পর্যালোচনা পেপার কিংবা সার্ভে গবেষণা। Original Article লেখা হয় মূল গবেষণার উপর ভিত্তি করে। আর মূল গবেষণার মধ্যে পরে, ল্যাবরেটরী ভিত্তিক গবেষণা, কম্পিউটার ব্যবহার করে গবেষণা, এই গুলোর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ক্ষেত্র হচ্ছে ডাটা সাইন্স ফিল্ড এবং সিমুলেশন রিসার্চ। মোট কথা হচ্ছে, যে কাজ করে আমি কোন ডাটা পাবো, তাই হচ্ছে মূল গবেষণা। এই কারণে এই সব ডাটাকে বলা হয় প্রাইমারি ডাটা। কিন্তু এইসব ডাটা যখন কোন জার্নালে পাবলিশ হয়, তখন অন্য কেউ যদি এই একই ডাটা দিয়ে অন্য কেউ তার কাজের পার্স্পেক্টিভে অন্য আরো ডাটার সাথে কাজে করে, তখন তা হয়ে যায় সেকেন্ডারি ডাটা। মজার বিষয় হলো এই সেকেন্ডারি ডাটা দিয়েই আমাদের রিভিউ পেপারের কাজ করতে হয়।” এজন্য গবেষণার প্রশ্ন বা Research Questions (RQs) গুলোকে লিখে রাখতে হবে। অনেকগুলো প্রশ্ন একসাথে লেখা যেতে পারে তবে কয়েকটি স্পেসিফিক প্রশ্নের উত্তর গবেষণায় খোঁজা হবে। এই প্রশ্নগুলোকেই একে একে উত্তর দেয়া হবে কনক্লুসন বা ডিসকাসন সেকশনে।
যখন আপনি সমস্যা বের বের করতে পেরেছেন তখন আপনাকে দেখাতে হবে আপনার গবেষণাটি কেন দরকার। অর্থাৎ আপনাকে বোঝাতে হবে আপনার রিসার্চের মোটিভেশন কী? সেজন্য এই সমস্যার উপর ইতোপূর্বে কীরকম কাজ হয়েছে এবং কাজগুলোকে আপনার তখন আপনাকে দেখাতে হবে আপনার গবেষণাটি কেন দরকার। অর্থাৎ আপনাকে বোঝাতে হবে আপনার রিসার্চের মোটিভেশন কী? সেজন্য এই সমস্যার উপর ইতোপূর্বে কীরকম কাজ হয়েছে এবং কাজগুলোকে আপনার রিভিউ করতে হবে। লিটারেচার রিভিউ লেখা সহজ নয়। মানে এটিকে খুব সহজ ভাবে নেয়া উচিত নয়। লিটারেচার রিভিউ সময় নিয়ে করতে হয় এবং রেফেরেন্স পেপারের জার্নালের মান, যে গ্রুপ থেকে কাজটি করা হয়েছে তাঁরা কতটা রিলায়েবল এটি মাথায় রাখতে হয়। এবং অবশ্যই প্রকাশিত কাজের অর্ডার ঠিক রেখে রিভিউ ওয়ার্ক করতে হয় ।
আপনি হয়তো খুব ভালো মানের মৌলিক কাজ করেছেন কিন্তু ভাল লিটারেচার রিভিউ না থাকার কারণে রিভিউয়াররা বাতিল করে দিতে পারে। এক্ষেত্রে আপনার স্টাডির মৌলিকতা ও অবদান তুলে ধরতে হবে।
3. Methodology
এই অংশে মূলত পরিসংখ্যানিক এনালিসিস করা হয়। একজন গবেষক নানা ভাবে তার গবেষণা করতে পারেন। এক্সপেরিমেন্টাল কাজ হলে স্যাম্পল প্রিপারেসন, এক্সপেরিমেন্টাল টেকনিক ইত্যাদি ডেসক্রাইব করা হয়। প্রথমেই বলে নেই, যে কোন গবেষণার জন্য অনেক ধরণের পরীক্ষিত টেকনিক থাকে, টেকনিকগুলো ডেসক্রাইব করার সময় উদাহরণ হিসেবে নিজের গবেষণার কোন উদাহরণ দিয়ে তা বিস্তারিত কোথায় কোন সেকশনে, কোন চ্যাপ্টারে আছে সেটা উল্লেখ করে একটি সংযোগ তৈরি করে দিতে হয়। তখন একজন রিডার এই সব টেকনিক্যাল ডেসক্রিপশন পড়েও তখন এক ধরণের শান্তি অনুভব করতে পারে। রসকষহীন টেকনিক্যাল বিষয়গুলি পড়তে এই শান্তি পাওয়াটা বিশেষ জরুরী। টেকনিকগুলোর মধ্যে তিনটি টেকনিক খুব পপুলার (বিস্তারিত জানতে wiki তে খুজুন):
• Cross-sectional study
• Observational study
• Experimental study
4. Analysis/Results
রেজাল্ট লিখতে গবেষণার অর্ডার ঠিক রাখতে হবে, একটি সাব-কন্টেন্ট এর সাথে অন্য সাব-কন্টেন্ট এর সংযোগ রাখতে হবে, অন্যথায় এটি খুব নিম্ন মানের থিসিস হবে। নিম্ন মানের পেপার কখনোই সাইট করা উচিৎ না। আর রেজাল্ট অ্যান্ড ডিসকাশন একাধিক চ্যাপ্টার হলে প্রথম চ্যাপ্টারের সাথে পরের চ্যাপ্টারের লিঙ্ক তৈরি করতে হবে , আর এটি ভালো কাজের বৈশিষ্ট্যও বটে।
ডেটা সংগ্রহের পর সেটিকে ডাটা ক্লিন/মাইনিং করে সামারি রেজাল্ট এবং পরিসংখ্যানের মডেল/মেশিন লার্নিং এলগোরিদম (যদি দরকার হয়) ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।
5. Discussion
আমার মতে, ডিসকাশন পার্টিটি সব চেয়ে জটিল একটি পার্ট। এখানে সম্পূর্ণ রিসার্চের সারমর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়। ডিসকাশন পার্টের উপর নির্ভর করে আপনার রিসার্চ কতটুকু কোয়ালিটিফুল। আপনার রিসার্চ ফাইন্ডিংস এর সাথে রিলেটেড কাজের রেজাল্ট দিয়ে comparison দেখিয়ে দিবেন। এবং Research Question ডিটেলস আলোচনা করে দেখাতে হয় আপনার ফাইন্ডিং এর সাথে আপনার এক্সপ্রিমেন্টাল রেজাল্ট এর মিল আছে কিনা ! এই অংশটি আপনার রিসার্চকে পুনরায় জাস্টিফাই করবে।
6. Conclusion
পেপার/থিসিসের কঙ্কলুসন (conclusion) আর এবসট্র্যাক্ট থিসিস/রিসার্চ পেপার শেষ হলেই লিখা উচিৎ। আর কঙ্কলুসন লিখতে গিয়ে অনেকেই সামারি লিখে ফেলে। সেক্ষেত্রে উপসংহারটিকে আপনার ডিসকাশন সেকশনের শেষ প্যারা হিসেবে লিখতে পারেন। অনেক জার্নালে কনক্লুশন এবং ডিসকাশন সেকশন দুটি একত্রে লেখা হয়। কনক্লুশন এ আপনার কাজের লিমিটেশন এবং ফিউচার কাজের প্রসেস তুলে ধরতে পারেন। আপনার কাজের সম্পর্কে অন্য রিসার্চাররা একটি কনসেপ্ট পেয়ে যাবে , হতেও পারে ভালো কোনো ল্যাবে আপনার কাজের জন্য অফারও পেয়ে যেতে পারেন।
রিসার্চ প্রোপোজাল যেভাবে লিখতে হবে
আমিনুর রহমানFebruary 6, 2019রিসার্চ প্রোপোজাল
রিসার্চ প্রোপ্রোজাল
কি এবং কেন?
রিসার্চ প্রোপ্রোজাল হচ্ছে এক ধরণের গবেষণা আউটলেট। কোন গবেষণা কিভাবে পরিচালিত হতে পারে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা। গবেষণার পদ্ধতি এবং প্রস্তাবনা।
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিএইচডি কোর্সে দরকার হতে পারে। জার্মানিতে কিছু মাস্টার্স কোর্সেও চাওয়া হয়ে থাকে। যদিও মাস্টার্স কোর্সের কারিকুলাম আগে থেকে নির্দিষ্ট, নিয়ম রক্ষার জন্য এবং অ্যাডমিশনের ক্রাইটেরিয়া হিসেবে রিসার্চ প্রোপ্রোজাল জমা দেওয়া অনেকটাই বাধ্যতামূলক। কেন্ডিডেটের রিডিং স্কিল, গবেষণা সম্পর্কে পূর্ব আইডিয়া সম্পর্কে ধারণা পাবার লক্ষ্যেও কিছু কোর্সে রিসার্চ প্রেপ্রোজাল জমা দিতে হয়। নিজের সাইন্টিফিক জ্ঞান সম্পর্কে অ্যাডমিশন কমিটির কাছে নিজেকে আলাদাভাবে চেনানোর অন্যতম মাধ্যম হতে পারে।
সাধারণ কিছু তথ্য
লেখা শুরুর আগে যেসব জ্ঞাতব্য বিষয়
আকারের দিক থেকে রিসার্চ প্রোপ্রোজাল ১৫০০ অধিক শব্দ অথবা ৪-১৫ পেইজের হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইউনিভার্সিটি অথবা গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে নির্দিষ্ট ওয়ার্ড লিমিট থাকতে পারে। সে মোতাবেক অনুসরণ করাই শ্রেয়। নির্দিষ্ট লে-আউট- টাইপফেস, ফন্টস এবং স্পেসিং থাকতে হবে। টেবিল অব কনটেন্ট এবং পেইজ নাম্বার থাকাও জরুরি।
গবেষাণার ধারণা নিজে নিজে লিখতে হবে এবং মৌলিক হতে হবে। আইডিয়া এবং তথ্য কপি পেস্ট করার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। সঠিক সাইটেশন সরবরাহ করা জরুরি। কোন কারনে নকল ধরা পড়লে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল।
টাইটেল পেইজ
গবেষণার শিরোনাম
টাইটেল পেইজের শুরুতেই গবেষণার নাম বা শিরোনাম থাকতে হবে। গবেষণার সাথে নামের সার্থকতা থাকতে হবে। পাশাপাশি ব্যক্তিগত কিছু তথ্য থাকবে। নাম, অ্যাকাডেমিক টাইটেল, ব্যাচেলর/মাস্টার্স ইউনিভার্সিটি, জন্মতারিখ, ইমেইল আইডি ইত্যাদি।
জেনারেল ওভারভিউ
এবং লিটারেচার রিভিউ
কি নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন ধারা বর্ননা থাকবে। পূর্ববর্তী গবেষণা/থিসিস অথবা কাজের কোন অভিজ্ঞতা থাকলে সেগুলো তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি জার্নাল পেপার ঘেঁটে উক্ত বিষয় সংক্রান্ত তথ্য লেখকের নামসহ উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রস্তাবনায় থিওরীটিক্যাল স্কোপ পরিষ্কার এবং যৌক্তিকভাবে আলোচনা করতে হবে।
প্রশ্ন এবং অবজেকটিভ
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
গবেষণার আউটলাইনে কি নিয়ে ‘অনুসন্ধান’ করা হবে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণী এবং সাইন্টিফিক প্রশ্ন উল্লেখ থাকতে হবে। সেই সাথে গবেষণা লক্ষ্য উদ্দেশ্য সুপষ্ট থাকা জরুরি। আপনার প্রস্তাবনায় আসন্ন গবেষণা কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন দরকারি- এই বিষয়গুলো উল্লেখ থাকবে।
মেথডোলজি
সাইন্টিফিক পদ্ধতি
প্রস্তাবনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মেথডোলজি। অ্যাডমিশন কমিটি এই অংশেই বেশি মনোযোগ দিতে পারে। পুরো প্রস্তাবনার সবচেয়ে দীর্ঘ অংশ বিশেষ। সাইন্টিফিক প্রশ্ন কিভাবে হ্যান্ডেল করা হবে সে সম্পর্কে আলোচনা। তথ্য এবং উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি, সাইন্টিফিক মেথড এবং অ্যানালাইসিস- এই বিষয়ে আলোচনা জুড়ে দিতে হবে। উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোন চ্যালেঞ্জ আসন্ন মনে হলে সে বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা জরুরি।
সময়সীমা
গবেষণার টাইমলাইন
পুরো গবেষণার টাইমলাইন ডিজাইন করতে হবে। কতোগুলো ফেইজে গবেষণা চলতে পারে এবং প্রত্যেক ফেইজে আনুমানিক সময় কেমন দরকার হবে- ইত্যাদি ক্যালকুলেশন থাকবে। হয়তোবা আপনার টাইমলাইন শতভাগ সফল হবে না। এই টাইমলাইনের মাধ্যমে আপনার প্রজেক্ট পরিকল্পনার দক্ষতা প্রকাশ পাবে।
প্রস্তবনায় যা থাকা জরুরি
গবেষণা প্রস্তাবনায় যা থাকতে হবে
Table of Contents
Abstract
Data Collection, Analysis and Evaluation
Introduction to the General Topic
Analysis of texts and documents
Problem Statement and Justification of the Research Project
Expected Results and Output of the Study
Hypothesis and Objectives of the Study
Bibliography
Literature and Research Review
Appendix, e.g. Tables, Graphs, Questionnaires etc.
Research Method(s)
Timetable of Data
বিশ্ব বার্তা নিউজ পোর্টাল: যারা ইতিমধ্যেই গবেষণা শেষ করে ফেলেছেন বা শেষ করার পথে তারা একটি ভাল গবেষণা পত্র কিভাবে লিখবেন, সেটা অবশ্যই জানেন। কিন্তু সমস্যা হল নতুন দেরকে নিয়ে, যারা গবেষনায় ঢুকবেন বা ঢোকার চেষ্টা করছেন। আজ আমরা জানব, একটি ভালো গবেষণা পত্র লেখার জন্য কি কি স্টেপ আপনি ফলো করবেন। কোনো পেপার লিখতে গেলে প্রথমেই মাথাতেই প্রশ্ন আসে ফরম্যাটিং কিভাবে করবো, রেফারেন্স কিভাবে দেব, কি কি সেকশন রাখবো, ফুটনোট কিভাবে আসবে ইত্যাদি। জার্নাল ভেদে গবেষণা পত্রের ফরম্যাটিং-এ কিছু কিছু পরিবর্তন হয়, তবে মূল কাঠামো সব জাগাতে একই থাকে।
গবেষণা পত্র লেখার প্রথমেই একটি আউট লাইন তৈরি করুন। যেমনঃ ১. টাইটেল ২. এবস্ট্রাক্ট ৩. কী-ওয়ার্ড ৪. ইন্ট্রোডাকশন ৫. বিষয় ভিত্তিক আলোচনা ৬. রেজাল্ট ও ডিস্কাশন ৭. একনলেজমেন্ট ৮. কনক্লুশন এবং ৯. রেফারেন্স। এরপর এই কাঠামো ধরে ধরে লিখতে থাকুন।
১.টাইটেল: জার্নাল পেপারের টাইটেল বা শিরোনাম দেওয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গবেষণা পত্রটি মূলত কি নিয়ে, সেটার উপরে বা কিছু স্পেসিফিক কি-ওয়ার্ড জুড়ে দিয়ে সুন্দর-সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিশ্লেষনাত্মক একটি প্রাসঙ্গিক শিরোনাম ঠিক করবেন। টাইটেলের নিচে অথর লিস্টে শিক্ষার্থীর নাম, সুপারভাইজারের নাম ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন অবদান যারা রেখেছেন তাদের নাম রাখতে হবে। এফিলিয়েশনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা এবং অথরদের ইমেইল আইডি এবং এড্রেস দিতে হবে।
2. এবস্ট্রাক্ট: এবস্ট্রাক্ট বা সারমর্ম হল মূল গবেষণার সংক্ষিপ্ত সার। সাধারনত ৫০০ বা তার কম শব্দের মদ্ধ্যেই পুরো সারমর্ম লিখতে হয়। জার্নালের গাইড লাইন অনুযায়ী, অবশ্যই আপনার পেপারের গুরুত্ব অনুসারে কিছু ভুমিকা দিতে হবে। এরপরে খুব সংক্ষেপে পেপারে মূল কি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, কি কি মেথড ব্যবহার হয়েছে তার উল্লেখ করতে হবে। রেসাল্ট-ডিস্কাশনের কিছু অংশও এখানে যুক্ত করা যেতে পারে।
3. কী-ওয়ার্ড: ৫/৬ টি শব্দ নির্বাচনের মাধ্যমে আপনার লেখাটির মূল বিষয় পরিস্কার করে ফেলতে হবে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক টার্ম, প্যামিটারেরগুলোর নাম কীওয়ার্ড হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। টাইটেল থেকেও কিছু মূল শব্দ এখানে লিখতে পারেন।
4. ইন্ট্রোডাকশন: ইন্ট্রোডাকশন হল রিসার্চ পেপারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইন্ট্রোডাকশনে সাম্প্রতিক রেফারেন্স যুক্ত আপনার গবেষণা রিলেটেড কিছু কাজ উল্লেখ করতে হবে, বিশেষ করে যেই জার্নালে পাঠাবেন- সেই জার্নালে প্রকাশিত কিছু পেপার অবশ্যই যুক্ত করবেন। এই অংশে লেখার স্কোপ, তাতপর্য, গুরুত্ব, উদ্দেশ্য, আপনার পেপারের মূল আলোচ্য সমস্যার বর্নণা করতে হবে।
৫. বিষয় ভিত্তিক আলোচনা: এই অংশটি রিসার্চ পেপারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আপনার রিসার্চ পেপারের রেজাল্টের প্যারামিটারগুলো এখানে বর্ননা করতে হবে। যেসব ইকুপমেন্ট-যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছে তার পরিচিতি ও বর্ননা এখানে দিতে হবে। আপনার রিসার্চ পেপারে যে মেথডলজি ব্যবহার করেছেন, সেটা এখানে উল্লেখ করতে হবে।
৬. রেজাল্ট ও ডিস্কাশন: এই সেকশনে গ্রাফ ও টেবিল রাখতে হবে। আপনি যে মেথডলজি ব্যাবহার করেছেন, তার বাস্তব রেজাল্ট এখানে উল্লেখ করতে হবে। প্রতিটি টেবিল ও গ্রাফের/চার্টের বর্ননা পাশাপাশি রাখতে হবে। ডিস্কাশনে প্রাসঙ্গিক কিছু পেপারের রেজাল্টের সাথে প্রদত্ত পেপারের রেজাল্টের তুলনা রাখলে ভালো হয়।
৭. কনক্লুশন: রেজাল্ট সেকশনে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ন তথ্য এইখানে পয়েন্ট আকারে লিখতে হবে। অবশ্যই কিছু নিউমেরিক্যাল রেজাল্ট থাকতে হবে, শুধু তুলনামূলক আলোচনা থাকলে চলবে না। আপনার পেপারের কি কি সীমাবদ্ধতা আছে তা এখানে উল্লেখ করবেন। এছাড়া এই পেপারের মেথডলজি ব্যাবহার করে ভবিষ্যতে কি কি কাজ করা যেতে পারে তা অবশ্যই উল্লেখ করবেন।
৮. একনলেজমেন্ট: আপনার ল্যাব এসিস্টেন্ট, সহকারী, পরামর্শদাতা, আর্থিক সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম এই সমস্ত কিছুই এই অংশে উল্লেখ করবেন।
৯. রেফারেন্স: এটি পেপারের একবারে শেষে উল্লেখ করতে হবে। রেফারেন্স লেখার অনেক পদ্ধতি আছে। আপনি যে জার্নালে পাঠাবেন, সেখানে কোন পদ্ধতিতে লিখতে বলছে সেটা ফলো করুন। যেমনঃ হার্ভার্ড, নাম্বারিং সিস্টেম। রেফারেন্স সাজানোর অনেক সফটওয়ার আছে, যেমনঃ END NOTE(http://www.endnote.com/ ), ProCite (http://www.procite.com/ ) ইত্যাদি।
থিসিস কিভাবে লেখা উচিত: কিছু পরামর্শ
ড. মোহাম্মদ আব্দুল বাছিত
থিসিস লেখার সময় ছাত্ররা জিজ্ঞেস করে, ‘স্যার, থিসিস এর কোন চ্যাপ্টার প্রথমে লিখবো, শেষে কি লেখবো?’ এই প্রশ্নগুলোর সর্বজনীন কোন উত্তর নেই। আমি তাদেরকে বলি, এক জীবনে একটি ডিগ্রীর জন্য একটাই থিসিস লিখবে, কাজেই এমন ভাবে লিখবে যেন শেষ বয়সে নিজের থিসিসটা হাতে নিয়ে নিজেই গর্ব করতে পারো। একটি থিসিস কয়েকটি ছোট গল্পের সমাহার নয়, এটি একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস, কাজেই যেভাবেই লিখো না কেন, একটি প্যারাগ্রাফের সাথে অন্য প্যারাগ্রাফের, আগের চ্যাপ্টারের সাথে পরের চ্যাপ্টারের সংযোগ থাকাটা অত্যাবশ্যকীয়।
|
সাধারণভাবে মাস্টার্স লেভেলের একটি থিসিস এর পাঁচটি চ্যাপ্টার থাকে, পিএইচডি লেভেলে সাতটির মতো। প্রথম চ্যাপ্টার ইনট্রোডাকশন এবং এই চ্যাপ্টারটি থিসিসের প্রাণ। একটি থিসিসের পুরো অবজেকটিভ খুব অল্প কথায় এইখানে লেখা হয় এবং পুরো থিসিসে কি আছে এই চ্যাপ্টারে তা খুব চমৎকারভাবে ডেসক্রাইব করা হয়। সুতরাং আমার মতে ইনট্রোডাকশন এর আরটিকুলেসন সবচেয়ে কঠিন, তাই শেষের দিকে ইনট্রোডাকশন লিখতে আমি ছাত্রদের পরামর্শ দেই। দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে মূলত থাকে কিছু টেক্সট এবং লিটারেচার রিভিউ। এই চ্যাপ্টারটি খুব সতর্কভাবে লিখতে হয়, টেক্সট যেন অবশ্যই থিসিসের বিষয়ের সাথে রিলেটেড হয়, অপ্রাসঙ্গিক টেক্সট সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। টেক্সট লেখার সময় অনেক সময় স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম ড্র করতে হয়, এইসব ডায়াগ্রাম নিজের ড্র করা উচিৎ, অন্য অথরের ডায়াগ্রাম কপি করা খুবই অন্যায়। লিটারেচার রিভিউ সময় নিয়ে করতে হয় এবং রেফারেন্স পেপারের জার্নালের মান, যে গ্রুপ থেকে গবেষণাটি করা হয়েছে তারা কতটা রিলায়েবল এটি মাথায় রাখতে হয়; এবং অবশ্যই প্রকাশিত কাজের অর্ডার ঠিক রেখে রিভিউ ওয়ার্ক করতে হয়।
থার্ড চ্যাপ্টারে, রিসার্চ মেথোডলজি লিখা হয়, এক্সপেরিমেন্টাল কাজ হলে স্যাম্পল প্রিপারেসন, এক্সপেরিমেন্টাল টেকনিক ইত্যাদি ডেসক্রাইব করা হয়। যে কোনো গবেষণার জন্য অনেক ধরণের পরীক্ষিত টেকনিক থাকে, কিন্তু এইখানে যে টেকনিক তুমি তোমার কাজে ঠিক যেভাবে ব্যবহার করেছ ঠিক ওইভাবে তুলে ধরতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের অনেকগুলো মুড থাকে, তোমার কাজের জন্য তুমি যে মুড ব্যবহার করেছ, ওইটাই তোমার কাজের প্রসঙ্গ টেনে এইখানে ডেসক্রাইব করা উচিৎ। এক্সপেরিমেন্টাল টেকনিকগুলো ডেসক্রাইব করার সময় উদাহরণ হিসেবে নিজের গবেষণার কোন উদাহরণ দিয়ে তা বিস্তারিত কোথায় কোন সেকশনে, কোন চ্যাপ্টারে আছে সেটা উল্লেখ করে একটি সংযোগ তৈরি করে দিতে হয়। তখন একজন রিডার এই সব টেকনিক্যাল ডেসক্রিপশন পড়েও তখন এক ধরণের শান্তি অনুভব করতে পারে। রসকষহীন টেকনিক্যাল বিষয়গুলো পড়তে এই শান্তি পাওয়াটা বিশেষ জরুরী।
এইবার আসি মূল চ্যাপ্টারে অর্থাৎ রেজাল্ট অ্যান্ড ডিসকাশন চ্যাপ্টার। মাস্টার্স লেভেলের থিসিস হলে রেজাল্ট অ্যান্ড ডিসকাশন লিখতে একটি চ্যাপ্টারই যথেষ্ট, পিএইচডি থিসিস হলে অন্তত তিনটি চ্যাপ্টার থাকতে পারে, তবে এইখানে ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম নেই। রেজাল্ট লিখতে গবেষণার অর্ডার ঠিক রাখতে হবে, একটি সাব-কন্টেন্ট এর সাথে অন্য সাব-কন্টেন্ট এর সংযোগ রাখতে হবে, অন্যথায় এটি খুব নিম্ন মানের থিসিস হবে। অনেক সময় আমরা নিজের রেজাল্ট সাপোর্ট করতে গিয়ে লিখি – “এজ ওয়াজ অলছো রিপোর্টেড ইন রেফারেন্স [xx]”। এইভাবে লিখা উচিৎ না, ঐ পাটিকুলার রেফারেন্সে কি স্যাম্পল ছিল, কি টেকনিক ফলো করা হয়েছিল, বিশেষ কোন প্যারামিটার যদি থাকে সেটা কি ছিল, তোমার স্যাম্পল, টেকনিক এবং ব্যবহৃত প্যারামিটারের সাথে সাদৃশ্য কতটুকু, এই বিষয়গুলো খুব অল্প কথায় উল্লেখ করে রেফারেন্স পেপারের সাপোর্ট নিতে হবে, অন্যথায় রিডার মিসগাইড হতে পারে। আগে যেভাবে বলেছি, সকল রেফারেন্স পেপার মানসম্পন্ন কি না তা সব সময় বিবেচনায় রাখতে হবে, নিম্ন মানের পেপার কখনোই সাইট করা উচিৎ না। রেজাল্ট অ্যান্ড ডিসকাশন একাধিক চ্যাপ্টার হলে প্রথম চ্যাপ্টারের সাথে পরের চ্যাপ্টারের মেলবন্ধন তৈরি করেই পরের চ্যাপ্টার শুরু করতে হবে যেহেতু এইটি একটি উপন্যাস।
থিসিসের কনক্লুশন আর এবসট্র্যাক্ট থিসিস শেষ হলেই লিখা উচিৎ, বিশেষ করে, থিসিস সাবমিশন এর ঠিক ২/১ দিন আগে সব কারেকশন শেষ হলে তখনই এবসট্র্যাক্ট লিখা উচিৎ। আর কনক্লুশন লিখতে গিয়ে অনেকেই সামারি লিখে ফেলে। ইচ্ছে করলে তুমি শেষ চ্যাপ্টারে একটি সাব-সেকশন দিয়ে শর্ট সামারি লিখতে পারো এবং তারপরের সাব-সেকশনেই কনক্লুশন লিখো। তোমার থিসিস এর বিশেষ বার্তা খুব সতর্কভাবে কনক্লুশনে লিখা উচিৎ, যাতে একজন রিডার থিসিস টি পড়ে মনে করে, এটাই তো জানতে চেয়েছিলাম, থিসিসের রেজাল্ট এই মেসেজটাকেই সাপোর্ট করে।
একজন গবেষকের জন্য মাস্টার্স, কিংবা পিএইচডি ডিগ্রিই শেষ না, কেবল শুরু, তাই থিসিস এর শেষে একটি ‘ফিউচার ওয়ার্ক প্ল্যান’ এর সাজেশন লিখতে হয়ে, এটা যেন লিখার খাতিরে লিখা না হয়। থিসিসে অসমাপ্ত কোন গবেষণা থাকলে তা নিকট ভবিষ্যতে কিভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে, এই গবেষণা করার সময় প্রাসঙ্গিক কোন নতুন আইডিয়া আসলে ভবিষ্যতে তা নিয়ে কিভাবে গবেষণা করা যাবে, করা হলে প্রত্যাশিত রেজাল্ট কি হতে পারে এবং সায়েন্টিফিক কম্যুনিটি কিভাবে লাভবান হবে, এই বিষয়গুলো অল্প কথায় ভালোভাবে এই সেকশনে ফুটিয়ে তুলতে হবে।
কেউ কেউ বলতে পারেন, এটি তো থিসিস, সায়েন্টিফিক পেপার নয়, এতো নিখুঁতভাবে লিখার দরকার কি? এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। নলেজ বেইজড সব কিছু নিখুঁতভাবে করতে হয়, এইখানে বিন্দুমাত্র ভুল করা, কিংবা অবহেলা করা একদম উচিৎ নয়, রিডারের জন্য এটি মারাত্মক ক্ষতিকর।
ছাত্রদের আবারো বলছি, সায়েন্টিফিক রাইটিং এর একটি নিজস্ব প্যাটার্ন আছে, নিজের রাইটিং স্কিল ডেভোলাপ করার এটি একটি বিশেষ সুযোগ, সবটুকু মেধা আর সামর্থ্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে তুমি তোমার থিসিস টা লিখো, রিওয়ার্ড আজ হউক কাল হউক তুমি পাবেই। সবার জন্য শুভ কামনা।
লেখকঃ ড. মোহাম্মদ আব্দুল বাছিত, অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, বুয়েট।
আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আন্ডারগ্র্যাড পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল কাজ করলেও, অনেক সময় দেখা যায় সচেতনতার অভাবে কিংবা সদিচ্ছার অভাবে তাদের গবেষণাগুলো কোনো ভালো কনফারেন্স কিংবা জার্নালে পাবলিশ হয় না। ভালোভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে শতকরা পাঁচ থেকে দশ ভাগ শিক্ষার্থী তাদের থিসিস পাবলিশ করে, আর অবশিষ্ট কাজ অবহেলায় অযত্নে পড়ে থাকে থিসিস আর্কাইভে। কিংবা তাদের সেই কাজটি নিয়ে পরে অন্য কেউ একটু ঘষামাজা করে আর পরিসরটা খানিক বৃদ্ধি করে নিজের নামে চালিয়ে দেয়।
কেন আপনার থিসিস পাবলিশ করবেন?
কথাটা বোধহয় এইভাবে বললে ভালো হয়– কেন পাবলিকেশনের উপযোগী থিসিস করবেন? খুব সহজে কথায় এর উত্তর হলো– পাবলিকেশনকে ভালো গবেষণা কাজের প্যারামিটার হিসেবে ধরা যায়– যদি না আপনি কোন ভুঁইফোড় কিংবা ভূয়া কোনো জার্নাল কিংবা কনফারেন্সে পাবলিশ করে না থাকেন। আর আপনি যদি ভবিষ্যতে কোনো সময়ে উচ্চশিক্ষার জন্য আগ্রহী হন তাহলে তা আপনাকে স্কলারশীপ পেতে অবশ্যই সাহায্য করবে। কেননা উচ্চ শিক্ষার পুরোটাই গবেষণাকেন্দ্রিক – এখানে যে একজন ভালো গবেষক হতে পারবে প্রফেসররা তাকেই খুঁজেন। কাজেই আপনার পাবলিকেশন প্রমাণ করবে যে গবেষণার কাজে আপনার হাতেখড়ি হয়ে গেছে।
কোথায় আপনার কাজ পাবলিশ করবেন? কনফারেন্স না জার্নাল
একজন আন্ডারগ্র্যাডের ছাত্রের এ ধরনের সিদ্ধান্তটা নেয়া বেশ কঠিন– তাই এক্ষেত্রে সুপারভাইজরের মতামতকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া উচিত। আপনার কাজ যদি মৌলিক হয় এবং মানেও খুব ভালো হয় তাহলে তা ন্যাচারের মত জার্নালেও পাবলিশ হওয়ার যোগ্য। জানামতে বাংলাদেশে এখন আন্ডারগ্র্যাড পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও ন্যাচারের মতো জার্নালে তাদের কাজ পাবলিশ করছে। কাজের মান অনুযায়ী আপনার কাজ আপনি চাইলে কনফারেন্স কিংবা জার্নাল– এই দুইয়ের যেকোনো একটিতে পাবলিশ করতে পারেন। তবে সাধারণত জার্নালের পাবলিকেশনকে বেশি গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। জার্নালে আপনার কাজ পাবলিশ করতে চাইলে তিনটি বিষয় এর দিকে খেয়াল রাখতে হবে:
১. জার্নালের স্কোপ
২. ইস্যু/বছর এবং
৩. ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর
কোনো জার্নালে আপনার পেপারটি পাঠানোর আগে তার স্কোপ জানাটা খুবই জরুরী। এর মানে হলো সেই জার্নালটি কোন কোন বিষয়ের উপর পেপার পাবলিশ করে থাকে। ধরা যাক– আপনি সিরামিক কম্পোজিট ম্যাটারিয়ালস নিয়ে কাজ করেন, এখন আপনি ঠিক করলেন আপনার কাজটি আপনি ম্যাটারিয়াল সায়েন্স রিলেটেড কোন ভালো জার্নালে পাঠাবেন। পাঠালেন ঠিকই, কিন্তু সিরামিক ম্যাটারিয়ালস সম্পর্কিত কাজ তাদের পাবলিকেশনের আওতায় পড়ে না। অন্যদিকে শুধুমাত্র সিরামিক কম্পোজিটের কাজ পাবলিশ করে এমন ভালো ভালো জার্নাল অনেক আছে। সেক্ষেত্রে এডিটর হয়তো আপনাকে একটি ইমেইল করে জানিয়ে দেবে যে, আপনার কাজটি তাদের জার্নালের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, আপনি অন্য কোথাও সাবমিট করুন। কাজেই কোনো জার্নালে পেপার সাবমিট করার আগে তার স্কোপ দেখে নেয়া অতি জরুরী, যাতে সময় নষ্ট না হয়।
আমরা প্রায় সবাই বিশেষত ব্যাচেলর কিংবা মাস্টার্সের শিক্ষার্থীরা চাই আমাদের থিসিসের কাজটি দ্রুত পাবলিশ হোক। সেজন্য একটি জার্নাল প্রতি বছর কয়টি ইস্যু পাবলিশ করে সেটা দেখে নেয়া উচিত। কিছু কিছু জার্নাল আছে বছরে ৪টি ইস্যু পাবলিশ করে। এর মানে তাদের প্রতি বছর প্রচুর পেপার দরকার হয়, এবং এদের সম্পাদনা ব্যবস্থাও দ্রুত, গড়ে তিন মাস। সুতরাং এ ধরনের জার্নালে পেপার সাবমিট করলে দেখা যাবে চার থেকে ছয় মাসের মধ্যে আপনার পেপারটি পাবলিশ হয়ে যাবে, যদি তা পাবলিকেশনের জন্য মনোনীত হয়।
অনেক জার্নাল হয়তো রিভিউ করতে পুরো এক বছর সময় নেয় আবার ভুঁইফোড় জার্নালগুলো দেখা যায় ১০ দিনের মাঝেই আপনার পেপার একসেপ্ট করে তার অনলাইন কপিও রিলিজ দিয়ে দিচ্ছে। সাধারণত ভুঁইফোড় জার্নালগুলো টাকা পেলেই পেপার পাবলিশ করে দেয়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গবেষণা করতে চান না কিন্তু প্রমোশনের জন্য তাদের ঠিকই পাবলিকেশন দেখাতে হয়। সেক্ষেত্রে তারা এইসব ভুঁইফোড় জার্নালে টাকা দিয়ে পাবলিশ করে থাকেন, যেখানে পেপার পাঠালেই দশ দিনের মাঝে একসেপ্টেড হয়ে যায় আর একশো ডলার দিলেই পেপার ছাপিয়ে দেয়। একশো ডলার বিনিয়োগে একরকম বিনা কষ্টে প্রমোশন বাগিয়ে নেয়া- এর চেয়ে ভাল বিনিয়োগ আর কোথাও পাওয়া যাবে না।
এরপরে আপনাকে দেখতে হবে, জার্নালটির ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর কেমন। সহজ বাংলায় ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর বলতে বোঝায়, প্রতি বছর কিংবা একটা নির্দিষ্ট সময়কালে কোনো জার্নালে পাবলিশ হওয়া পেপার কতবার অন্য কোনো পেপারে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– কোনো জার্নালের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর যদি পাঁচ হয় তাহলে সেখানে পাবলিশ হওয়া পেপার বছরে গড়ে পাঁচটি করে সাইটেশন পায়। তবে হাই ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরের জার্নালে পাবলিশ করার জন্য কাজ মৌলিক হওয়া চাই, নতুবা আপনার পেপার রিজেকশনের সম্ভাবনাই বেশি। তাই যারা গবেষণার জগতে একদম নতুন তারা চাইলে শুরুতে কম ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরের জার্নালে পেপার পাবলিশ করতে পারেন, যেন উচ্চশিক্ষার্থে আবেদনের সময় আপনার অন্তত একটি পাবলিকেশন হলেও থাকে। আর ভবিষ্যতে আপনার মাস্টার্স, পিএইচডি এবং পোস্ট-ডকের সময় দেখা যাবে আপনার কাজের মান অনুযায়ী হাই ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরের জার্নালে আপনার পাবলিকেশন হয়ে গিয়েছে।
অন্যদিকে জার্নালের তুলনায় কনফারেন্সে পাবলিশ করা তুলনামূলক সহজ। তাই আপনার কাজ যদি ছোট পরিসরে হয়ে থাকে তাহলে আপনি কনফারেন্সেও আপনার পেপার পাবলিশ করতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে সেটি আন্তর্জাতিক মানের কনফারেন্স কিনা। নামের আগে হিরো থাকলেই যেমন হিরো হওয়া যায় না, ঠিক তেমনই নামের আগেই ইন্টারন্যাশনাল বসালেই গুণে ও মানে সেই কনফারেন্স আন্তর্জাতিক মানের হয়ে যায় না। ভুঁইফোড় ধরনের কনফারেন্স চেনার সবচেয়ে বড় উপায় হলো– এর অর্গানাইজিং কমিটি এবং এডভাইজার বোর্ডে কারা কারা আছেন তা ভালোভাবে দেখা।
সবার আগে দেখুন অর্গানাইজিং কমিটির মেম্বাররা ভালো গবেষক কিনা, তাদের নিয়মিত পাবলিকেশন হয় কিনা, এবং কমিটিতে বাইরের দেশের কোন কোন গবেষক যুক্ত আছেন, তারা সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপরিচিত কিনা। বাইরের দেশেও প্রচুর আজেবাজে ইউনিভার্সিটি আছে, সুতরাং বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ফ্যাকাল্টির নাম দেখলেই উৎফুল্ল হওয়ার কিছু নেই। এরপর দেখুন এডভাইজর বোর্ডে কারা আছেন। এই জায়গাটিতেই শুভংকরের ফাঁকিটা বেশি হয়। সমস্যা হলো এই ফাঁকি ধরার সুযোগ কম থাকে। প্রথমত, এডভাইজর কমিটি মেম্বাররা মোটামোটি ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এবং ফ্যাকাল্টিদের নাম যুক্ত করে দেয়। যাদের নাম যুক্ত করা হয় তারা হয়তো সেটা জানেও না।
এজন্য খেয়াল করে দেখবেন অনেকসময় তাদের পুরাপুরি রেফারেন্স দেয়া হয় না, তাই সন্দেহ হলে তাদের মেইল করে দেখতে পারেন যে তিনি আসলেই এই কনফারেন্সের সাথে যুক্ত কিনা। এরপর দেখবেন স্কোপ অব কনফারেন্স– অর্থাৎ কনফারেন্সটি নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের উপর ফোকাসড কিনা। যেমন– ম্যাটারিয়ালস রিসার্চ নিয়ে কনফারেন্স হলে সেখানে শুধু ম্যাটারিয়ালস ডেভেলপমেন্ট এবং ক্যারেক্টারাইজেশনের উপরই সেশন থাকবে, সেইখানে ফ্লুইড কিংবা থার্মাল ঢুকে যাবে না। অর্থাৎ ম্যাটারিয়াল এর থার্মাল প্রোপার্টিজ নিয়ে কেউ হয়তো কোন কিছু প্রেজেন্ট করতে পারে সেই সেশনে, তার মানে এই না যে সেই কনফারেন্সে গ্যাস টারবাইন ডিজাইন নিয়ে কেউ কথা বলবে।
এরপর দেখবেন কনফারেন্সের একসেপ্টেন্স রেট কেমন কিংবা তাদের রিভিউ প্রসেস আছে কিনা। ভালো ভালো কনফারেন্সে সাবমিট করা পেপার নূন্যতম এক থেকে দুই জন রিভিউয়ার দিয়ে রিভিউ করানো হয়, এবং সেখানে সব পেপার একসেপ্টডও হয় না, এমনকি ওরাল সেশনেও দেখা যাবে সবার এবস্ট্রাক্ট প্রেজেনেটশনের জন্য একসেপ্ট করা হয় না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওরাল প্রেজেন্টেশনকে পোস্টার প্রেজেন্টেশনে পাঠিয়ে দেয়া হয়।
আর কনফারেন্সে পাবলিশড হওয়া পেপারগুলো কোনো আন্তর্জাতিক মানের অনলাইন প্রসিডিং যেমন– AIP, IEE, ScienceDirect এর অধীনে পাবলিশ হয় কিনা তা-ও দেখবেন। এছাড়া দেখবেন কনফারেন্সের বিভিন্ন সেশনে ইনভাইটেড প্রেজেন্টেশনের সংখ্যা কেমন এবং কারা সেই প্রেজেন্টেশনগুলো দিচ্ছেন। যদি দেখেন ভালো ভালো গবেষক এসে কী-নোট স্পীকার হিসেবে আমন্ত্রণ পাচ্ছেন তাহলে বুঝবেন সেই কনফারেন্সে পেপার সাবমিট করা যায়।
থিসিস থেকে পেপার লেখার নিয়ম-কানুন
থিসিস লেখা হয়ে গেলে সেটিকে পেপারে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া খানিকটা সহজ। মূল লেখাটি লেখাই আছে, শুধু সেটিকে কেটে ছেটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো নিয়ে একতি পেপারে রূপ দিতে হবে। আপনার লেখা পেপারে কী কী পয়েন্ট থাকবে তা শুরুতে ঠিক করে নিন:
১. এবস্ট্রাক্ট
২. ইন্ট্রুডাকশন
৩. রিসার্চ মেথডস (ম্যাথমেটিকাল মডেলিং, এক্সপেরিমেন্টা ডিটেইলস)
৪. রেজাল্ট
৫. ডিসকাশন
৬.কনক্লুশন
৭. একনলেজমেন্ট
৮. রেফারেন্স
শুরুতে জার্নাল কিংবা কনফারেন্সে পেপার সাবমিশনের গাইডলাইন ভালোভাবে পড়ে নিন– যেমন, এবস্ট্রাক্ট কত শব্দের মধ্যে হতে হবে, ইমেজের সাইজ কেমন হবে, রেফারেন্সের নিয়ম ইত্যাদি। পেপারের টাইটেল এবং এবস্ট্রাক্ট এ দুটি লেখার পিছনে যথেষ্ট সময় ব্যয় করুন। শিরোনামটি যেন খুবই স্পেসিফিক হয় এবং এবস্ট্রাক্ট-এ সংক্ষেপে পেপারে মূল কী সমস্যা নিয়ে কাজ করা হয়েছে, কীভাবে করা হয়েছে এবং ফলাফল কী তা লিখতে হবে। এবস্ট্রাকট লেখার সময় লক্ষ্য রাখবেন যেন প্রাসংগিক কী-ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়। কেউ যদি আপনার রিসার্চের বিষয়টি নিয়ে কী-ওয়ার্ড দিয়ে সার্চ দেয় তাহলে আপনার পেপার এর তথ্য যেন শুরুর দিকেই আসে।
কোনো গল্পের শুরুটা যদি আকর্ষণীয় না হয়, তা যেমন গল্পের শ্রোতা কিংবা পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারে না, পেপারের ভূমিকাও ঠিক তেমনই– এটি আপনার গবেষণার সম্পর্কে গল্প বলার প্রথম ধাপ। কাজেই ইন্ট্রুডাকশনে অবশ্যই আপনার কাজের পরিধি, গুরুত্ব, সমসাময়িক কাজের সাথে আপনার কাজের পার্থক্য, আপনি কোন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করে কাজটি করেছেন এবং আপনার কাজের ফলাফল সবই সংক্ষেপে উল্লেক করা চাই। আর অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক যত বেশি পারা যায় সমসাময়িক গবেষণার কাজের রেফারেন্স দিয়ে তাদের সাথে আপনার কাজের পার্থক্যটা কোথায়, এবং কেন আপনার কাজ গুরুত্বপূর্ণ সেটি বলার চেষ্টা করবেন।
এরপর রিসার্চ মেথডলোজী, রেজাল্ট, ডিসকাশন এবং কনক্লুশন নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। আপনার থিসিস থেকেই পুরাটা কপি পেস্ট করতে পারেন, তবে একটু সংক্ষিপ্ত আকারে।
তবে রেজাল্ট ও ডিসকাশনে আপনার গ্রাফে সঠিকভাবে লিজেন্ডের ব্যবহার করবেন যাতে করে কেউ রেজাল্ট সেকশনের বর্ণনার সাথে গ্রাফকে সহজেই মেলাতে পারে। একটি গ্রাফে মাল্টিপল প্লট থাকে, ভিন্ন ভিন্ন কালার এবং ভিন্ন ভিন্ন লাইন টাইপ ও সিম্বল ব্যবহার করুন, এবং যখনই সেই গ্রাফও প্রদর্শিত ফলাফল নিয়ে লিখবেন তখনই গ্রাফের কোন লাইন, কোন সিম্বল কী ধরনের তথ্য রিপ্রেজেন্ট করে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিন। গ্রাফ এবং টেবিলের ক্যাপশনেও বিস্তারিত লিখুন।
একাধিক প্লট থাকলে কোন প্লট, কোন লাইন ইত্যাদি কী ধরনের তথ্য রিপ্রেজেন্ট করে তা লিখুন। টেবিলেও ঠিক একইভাবে বিভিন্ন কলামের হেডিং যথাযথভাবে লিখুন। যদি আপনার কাজ এক্সপেরিমেন্টাল হয় এবং তাতে যদি ভিন্ন ভিন্ন স্যাম্পল থাকে তাহলে পেপারে মূল বর্ণনা লেখার সময় সেইগুলোকে বিভিন্ন সাংকেতি নাম যেমন– AS001, AS002; এইভাবে চিহ্নিত করে টেবিলে স্যাম্পল ডিটেইলসের কলামে শুধু সাংকেতিক নামটি দিতে পারেন।
সবশেষে একনলেজমেন্ট এবং রেফারেন্স সেকশন। একনলেজমেন্টে আপনার গবেষণা কাজে কারা সাহায্য করেছে, কোনো সংস্থা যদি আপনার গবেষণার কাজটি স্পন্সর করে থাকে তাহল তাদের নাম এবং আপনার বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা যেই প্রতিষ্ঠানে থেকে আপনি এই কাজটি করেছেন তাদের কথা এই সেকশনে উল্লেখ করুন। আর রেফারেন্স সেকশনে আপনি যেসব পেপার থেকে সাহায্য নিয়েছেন তার সবগুলোর বিস্তারিত শিরোনাম উল্লেখ করুন।
প্রতিটি জার্নাল কিংবা কনফারেন্সের পেপারের রেফারেন্স সেকশন এর কিছু স্পেসিফিক ফরম্যাট থাকে– সেইটি অনুসরণ করুন। লেখা শেষ হয়ে গেলে, পুরো পেপারটি ভালোভাবে রিভিউ করুন– যাতে কোনো ধরনের ভূল না থাকে। প্রয়োজন হলে অন্তত দুই তিনজনকে পড়তে দিন– কারণ একজনের পড়ায় সব ভূল ধরা পড়ে না সাধারণত।
পেপার সাবমিশনের প্রক্রিয়া
আপনার পেপারটি প্রুফ রিড করা হয়ে গেলে যে জার্নালে কিংবা কনফারেন্সে সাবমিট করতে চান তাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে একাউন্ট খুলে ফেলুন, এবং সকল অথর, আপনার এবং অন্যান্য অথরের ইন্সটিউশন, ইমেইল এড্রেস, অথর এর ক্রম, এবং করেসপন্ডিং অথরকে হবেন তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করুন। তবে সাবমিশনের সময় আপনাকে সবকিছু আলাদা আলাদাভাবে সাবমিট করতে হবে। যেমন– আপনার মূল লেখাটি একটি ওয়ার্ড ফাইলে, এরপর যদি টেবিল থেকে তাহলে তা অন্য একটি ডকুমেন্টে, সকলপ্রকার চিত্র কিংবা গ্রাফ পৃথকভাবে এবং সেই সাথে রেফারেন্স অন্য আরেকটি ওয়ার্ড ফাইলে সাবমিট করতে হবে। চিত্র কিংবা গ্রাফ কী ফরম্যাটে চায় সেটি ভালো করে দেখুন এবং সে অনুযায়ী আপনার পেপার এ বর্ণনার ক্রমানুসারে আপলোড করুন। যদি আপনার গ্রাফ .eps কিংবা .pdf ফরম্যাটে সাবমিট করে থাকেন তাহলে ভালো করে প্রিভিউতে দেখে নিন সবধরনের সিম্বল ঠিক মতো আছে কিনা।
সবকিছু ঠিক থাকলে একটি কভার লেটার লিখুন, যেখানে ফরমালি এডিটরকে আপনার পেপারটি পাবলিশ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে একটি লিখবেন, এবং এই কভার লেটারটি সহ আপনার পেপারটি সাবমিট করুন।
পেপার সাবমিশনের পর
ছেলে-মেয়ের মাঝে এংগেইজমেন্ট হলেই যেমন শতভাগ বিয়ের গ্যারান্টি থাকে না, ঠিক তেমনই পেপার সাবমিশন করলেই যে পেপার এক্সেপ্টেড হবে এমন কোনো গ্যারান্টি পাওয়া যায় না। পেপার সাবমিশন করা হলে, শুরুতে জার্নালের এডিটর কিংবা সংশ্লিষ্ট কেউ একবার টেকনিকাল চেক করেন– মূলত এখানে দেখা হয় পেপারের বিষয়বস্তু জার্নালের স্কোপের মাঝে পড়ে কিনা এবং জার্নালের গুণগত মানের সাথে পেপারের গুণগত মানের সামঞ্জস্যতা আছে কিনা। এডিটর যদি মনে করেন আপনার পেপার এই দুই ফিল্টারের মধ্য দিয়ে যেতে পারেনি, তাহলে শুরুতেই আপনাকে জানিয়ে দেবেন যে আপনার পেপারটি তাদের জার্নালে পাবলিশ করা সম্ভব হচ্ছে না।
প্রথম ধাপ যদি আপনার পেপার অতিক্রম করতে পারে, তাহলে আপনার পেপার রিভিউয়ার দের কাছে পাঠানো হবে। জার্নালগুলাতে সাধারণত রিভিউয়ারদের সাজেশন চাওয়া হয়– তবে আপনি রিভিউয়ার হিসেবে যাদের নাম দেবেন তাদের কাছেই যে এডিটর পেপারটা পাঠাবেন তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিছু কিছু রিভিউয়ার আছেন যারা কাজের ব্যাপারে খুবই খুঁতখুঁতে, তাদের কাছে পেপার পড়লে প্রশ্নবাণে তারা আপনাকে জর্জরিত করে ফেলবে। কিছু রিভিউয়ার একদম শান্ত শিষ্ট লেজ বিশিষ্ট– দেখা যাবে দুই থেকে তিনটি ছোট ছোট প্রশ্ন করে শেষে বলে দিয়েছে আপনার কাজটি ভালো হয়েছে। রিভিউয়ারদের রিভিউয়ের ধরনের উপর ভিত্তি করে আপনার পেপারটি পাবলিশ করা হবে কিনা তার চার ধরনের রিপ্লাই আপনি পেতে পারেন।
১. এক্সেপ্টেড
২. এক্সেপ্টেড উইথ মাইনর কারেকশন
৩. এক্সেপ্টেড উইথ মেজর কারেকশন
৪. রিজেক্টেড বা বাতিল
ধরলাম, আপনার পেপারটি তিনজন রিভিউয়ার রিভিউ করেছেন, যদি দুইজন মাইনর কারেকশন দেন আর একজন বলেন এক্সেপ্টেড তাহলে আপনি পড়ে যাবেন দুই নং ক্যাটাগরিতে– অর্থাৎ আপনার পেপারের সামান্য কিছু জায়গায় ঘষা মাজা করা লাগবে। যদি দুইজন মেজর কারেকশন দেন আর একজন মাইনর কারেকশন তাহলে আপনি পড়বেন তিন নং ক্যাটাগরিতে– এর মানে হলো আপনাকে অনেক জায়গায় রিভিউয়ারদের মতামত অনুযায়ী পরিবর্তন করতে হবে, এবং পুনরায় সাবমিশনের পর যদি রিভিউয়ারদের পছন্দ না হয় তাহলে আপনার পেপার বাতিল এর খাতায় ফেলে দেয়া হবে।
আপনি গবেষণার জগতে একদম নতুন, আন্ডারগ্র্যাড কিংবা গ্র্যাড স্টুডেন্ – এজন্য আপনি কোনো ছাড় পাবেন না। হ্যাঁ তবে ছাত্র হলে কনফারেন্সের প্রেজেন্টেশন গুলাতে লোকজন প্রশ্ন কম করে– এই যা সুবিধা। আপনি মেজর কারেকশন কিংবা মাইনর কারেকশন যেইটাই পান না কেন– আপনাকে রিভিউয়ারদের প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। এজন্য যদি আপনার পেপারে নতুন কোনো গ্রাফ কিংবা ডাটা যুক্ত করার প্রয়োজন হয় তা-ই আপনাকে করতে হবে। অনেকসময় প্রফেসরদের পোস্ট ডক কিংবা পি এইচ ডি স্টুডেন্টরাও তাদের হয়ে আপনার পেপার রিভিউ করতে পারেন– এবং তাদের অভিজ্ঞতা কম থাকায় হয়তো অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নও করে বসতে পারে।
এক্ষেত্রেও ভদ্রভাবে উত্তর দিন– মনে রাখবেন, কোনোভাবে রিভিউয়ারকে আক্রমণ করা যাবে না। আর রিভিউয়ের প্রশ্নসমূহের জবাব আলাদা একটি ফাইলে জমা দিতে হয়। সেসব প্রশ্নের সাপেক্ষে আপনার পেপারে যদি নতুন কিছু যোগ করেন কিংবা পেপারের যে সেকশনের প্যারাতে সেই প্রশ্নের উত্তর আছে সেই প্যারাগুলো ভিন্ন ভিন্ন কালার দিয়ে হাইলাইট করেন এবং রেসপন্স লিস্ট এ সেইটি উল্লেখ করুন। আর যদি জার্নাল কোন কারণে রিজেক্ট হয় তাহলে আপনার কাজটি আবার রিভিউ করুন, কোনোকিছু পরিবর্তন করা দরকার হলে তা-ই করুন। এরপর অন্য কোনো জার্নালে পাঠিয়ে দিন, তা পাবলিশ করার জন্য।
বাইরে পড়তে যেতে আপনাকে রিসার্চ এর বেসিক ও পেপার রাইটিং নিয়ে বিস্তারিত জানতে হবে। সাথে যদি কোনো পাবলিকেশন থাকে তা আপনার স্কলারশিপ প্রাপ্তিতে এক্সট্রা বেনেফিট দিবে।
রিসার্চ লার্নিং থেকে পেপার পাবলিকেশন পর্যন্ত সাপোর্ট নিয়ে আপনার জন্য রয়েছে মাস্টারকোর্স। বিস্তারিত জানতে ভিজিট https://cutt.ly/RSRM
All reactions:
18