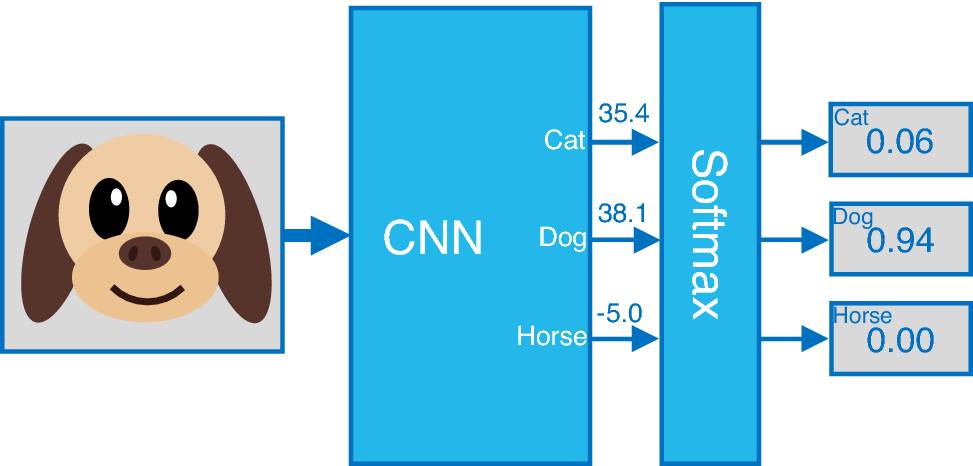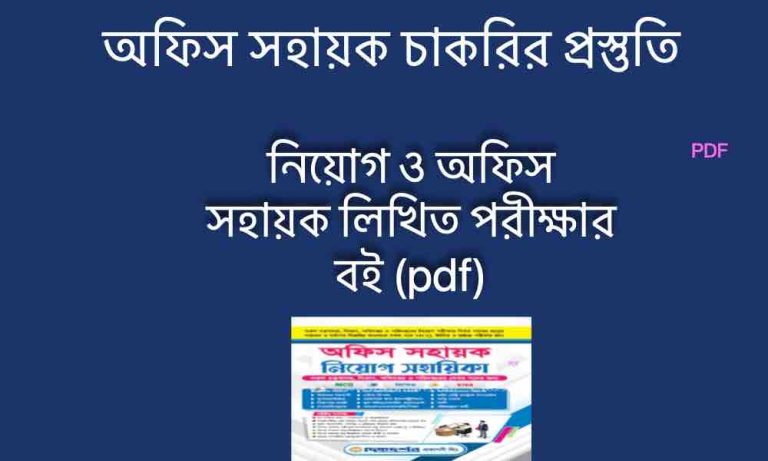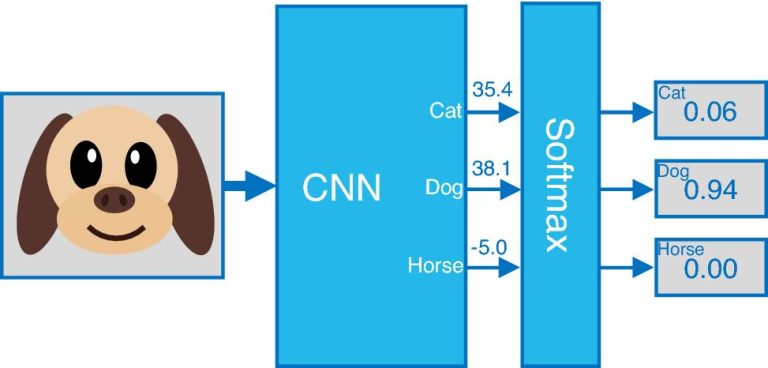Logistic Regression (লজিস্টিক রিগ্রেশন)
Logistic Regression (লজিস্টিক রিগ্রেশন)
=========================
.
একটা ছোট্ট গল্প দিয়ে শুরু করা যাক।
.
ধরো, তুমি একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক, বহু বছর ধরে ছাত্রছাত্রীদের পড়াচ্ছো। তোমার ক্লাসে এমন একজন ছাত্র আছে, যার নাম রাহাত। রাহাত পড়াশোনায় মোটামুটি, কিন্তু তার একটুখানি অনিয়মিত অভ্যাস আছে—কখনো পড়াশোনার জন্য রাত জেগে পরিশ্রম করে, আবার কখনো দীর্ঘদিন ধরে বই-খাতা খুলেও দেখে না। পরীক্ষার আগে সে খুব টেনশনে থাকে, কারণ সে জানে না, পাস করবে কিনা। এবার তুমি তাকে সাহায্য করতে চাও।
.
তুমি ভাবছো, তুমি তো বছরের পর বছর ধরে ছাত্রছাত্রীদের তথ্য সংরক্ষণ করেছো। তাদের পড়াশোনার সময়, ক্লাসে উপস্থিতি, পূর্বের ফলাফল ইত্যাদি তোমার কাছে আছে। তাহলে কেন এই ডেটার উপর ভিত্তি করে রাহাতের পরীক্ষায় পাস করার সম্ভাবনা বের করার চেষ্টা করছো না?
লজিস্টিক রিগ্রেশন কীভাবে সাহায্য করবে?
———————————————
এখানে আসে লজিস্টিক রিগ্রেশন। এটা এমন একটি টুল যা ব্যবহার করে তুমি বুঝতে পারবে, রাহাতের মতো একজন ছাত্র পরীক্ষায় পাস করতে পারে কিনা। তুমি তার পড়াশোনার সময়, ক্লাসের উপস্থিতি এবং পূর্বের পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে তার সম্ভাবনা বের করতে পারবে।
তবে এই মডেল “পাস করবে” বা “ফেল করবে” সরাসরি এভাবে বলে না। এটি বলে, “রাহাতের পাস করার সম্ভাবনা ৮৫%”। যদি ৫০% এর বেশি সম্ভাবনা পাওয়া যায়, তুমি বলতেই পারো, “রাহাত, তুমি সম্ভবত পাস করবে!”
.
গল্পের আরেকটি উদাহরণ:
=================
.
এবার আরেকটা গল্প বলি। ধরো, তোমার ছোট বোন নীলা একটা নতুন গাড়ি কিনতে চায়। কিন্তু সে খুব চিন্তিত, কারণ গাড়িটি কিনলে তা তার জন্য লাভজনক হবে কিনা, সেটা নিয়ে সন্দেহে আছে। সে তার বাজেট, গাড়ির মাইলেজ, এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচ নিয়ে খুব ভাবছে।
এখন তুমি, তার বড় ভাই বা বোন হিসেবে, চাও তাকে একটি যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে। তোমার কাছে নীলার এই তথ্যগুলো আছে—বাজেট, মাইলেজ, এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচ। তুমি লজিস্টিক রিগ্রেশন ব্যবহার করে তাকে সাহায্য করতে পারো, মডেল করে বোঝাতে পারো যে এই গাড়ি কেনা তার জন্য লাভজনক হবে কিনা। মডেল হয়তো বলবে, “৭০% সম্ভাবনা আছে যে গাড়িটি কেনা লাভজনক হবে।”
.
কেন লজিস্টিক রিগ্রেশন?
—————————
কারণ, এমন অনেক সিদ্ধান্ত আছে যেখানে ফলাফল সোজাসুজি “হ্যাঁ” বা “না” তে আসে না। অনেকগুলো ফ্যাক্টর একসঙ্গে কাজ করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। লজিস্টিক রিগ্রেশন সেই ফ্যাক্টরগুলোকে বিশ্লেষণ করে এবং একটি সম্ভাব্য ফলাফল দেয়, যা তোমার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
.
উপসংহার:
যেমন রাহাতের পাস বা ফেল করা এবং নীলার গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত, এই ধরণের পরিস্থিতিতে লজিস্টিক রিগ্রেশন খুব কার্যকর। এটি বিভিন্ন ফ্যাক্টরকে একত্রে বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্যতা দেয়, যা থেকে তুমি তোমার সিদ্ধান্ত নিতে পারো।
তাহলে তুমি লজিস্টিক রিগ্রেশনকে এমন এক বন্ধুর মতো ভাবতে পারো, যে তোমার সামনে সম্ভাব্যতা তুলে ধরে এবং বলে, “দেখো, এই ফলাফলটি হওয়ার সম্ভাবনা এতো শতাংশ, তুমি সিদ্ধান্ত নাও!”
.
.
গুগল অ্যালগরিদম এর সাথে Logistics regression এর সম্পর্ক
===================================
গল্পের শুরু:
একটা সময় ছিল যখন গুগল মোটামুটি নতুন ছিল। ধরো, একসময় ছোট ছেলে বা মেয়ে যখন ইন্টারনেটে কিছু খুঁজতে যেত, তারা গুগলে “সেরা চকলেট কেকের রেসিপি” লিখে সার্চ দিতো। কিন্তু তখন তারা বিভিন্ন রকমের ফলাফল পেতো, যার মধ্যে কিছু হয়তো সত্যি চকলেট কেকের রেসিপি ছিল, আর কিছু একেবারেই সম্পর্কহীন। গুগল তখন ঠিক বুঝতে পারছিল না কোনটা সত্যিকারের ভালো রেসিপি, আর কোনটা নয়।
গুগলের চ্যালেঞ্জ:
——————-
.
.
গুগলের তখন একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল—কীভাবে তারা ব্যবহারকারীদের এমন ফলাফল দিতে পারে যা সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক? তারা ভাবলো, “আমরা কি ব্যবহারকারীর অনুসন্ধানের ফলাফলগুলোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক খুঁজে বের করতে পারি? ব্যবহারকারীর আচরণ দেখে কি বোঝা সম্ভব যে কোন লিংকগুলো মানুষ বেশি পছন্দ করছে?”
এখন, এখানে আসে লজিস্টিক রিগ্রেশন।
.
গল্পের রিলেট:
—————
ধরো, তুমি যেমন রাহাতের পরীক্ষার ফলাফল ভবিষ্যদ্বাণী করতে চেয়েছিলে, ঠিক তেমনই গুগলও চায় ভবিষ্যদ্বাণী করতে—কোন ওয়েবসাইটের লিংক ব্যবহারকারীদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হতে পারে। এবার লজিস্টিক রিগ্রেশন গুগলকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে?
গুগল কীভাবে লজিস্টিক রিগ্রেশন ব্যবহার করে?
==============================
.
গুগল প্রতিটি ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ফ্যাক্টর বিশ্লেষণ করে, যেমন:
কতজন মানুষ সেই লিংকে ক্লিক করছে।
লিংকে ঢুকে কতক্ষণ সময় কাটাচ্ছে।
লিংকটি কতজন শেয়ার করছে।
এই ফ্যাক্টরগুলো দেখে গুগল ভবিষ্যদ্বাণী করতে চায়, একটি লিংক কতটা প্রাসঙ্গিক বা গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু গুগলের কাজ একটি নির্দিষ্ট সার্চের জন্য “প্রাসঙ্গিক” এবং “অপ্রাসঙ্গিক” লিংক আলাদা করা, তারা লজিস্টিক রিগ্রেশন ব্যবহার করে এটা করতে পারে। তারা প্রতিটি লিংকের জন্য একটি সম্ভাব্যতা নির্ধারণ করে যে এই লিংকটি কতটা প্রাসঙ্গিক (উদাহরণস্বরূপ, ৭৫% সম্ভাবনা যে এই লিংকটি ব্যবহারকারীর খোঁজা তথ্যের জন্য উপযুক্ত)।
.
রাহাতের উদাহরণে ফিরে যাই:
===================
.
তুমি যেমন রাহাতের পড়াশোনা, উপস্থিতি এবং পূর্বের পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে তার পাস বা ফেলের সম্ভাবনা নির্ধারণ করেছিলে, ঠিক তেমনই গুগলও সার্চের ক্ষেত্রে লজিস্টিক রিগ্রেশন ব্যবহার করে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের সম্ভাব্যতা নির্ধারণ করে। যদি কোনো ওয়েবসাইটের সম্ভাব্যতা বেশি হয়, তাহলে গুগল সেটিকে প্রথমে দেখায়।
গল্পের শেষাংশ:
.
তুমি ছাত্রছাত্রীদের বোঝালে, গুগল আসলে ঠিক তোমার মতোই বিশ্লেষণ করে। তুমি যেমন ছাত্রের বিভিন্ন আচরণ দেখে তার পাস করার সম্ভাবনা বের করো, গুগলও তেমনি বিভিন্ন ফ্যাক্টর বিশ্লেষণ করে দেখায় কোন ওয়েবসাইট সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত।
.
লজিস্টিক রিগ্রেশন এখানে সেই সেতুবন্ধনের কাজ করে, যা ব্যবহার করে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়—একটি ওয়েবসাইট কি ব্যবহারকারীর জন্য সঠিক ফলাফল দেবে কিনা, ঠিক যেমন তুমি রাহাতের পাস করার সম্ভাবনা নির্ধারণ করেছিলে।
logistics regression কিভাবে প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়কে পৃথক করে
=======================================
.
লজিস্টিক রিগ্রেশন প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোকে কীভাবে পৃথক করে তা বুঝতে গেলে প্রথমে এর কাজ করার পদ্ধতি একটু সহজ করে বলা যাক।
.
কল্পনা করো:
ধরো, তুমি একজন শিক্ষক, আর তোমার সামনে একটা প্রশ্ন—“তোমার ছাত্র রাহাত পাস করবে নাকি ফেল করবে?” এখন তুমি অনেকগুলো তথ্য সংগ্রহ করেছো: রাহাতের পড়াশোনার সময়, ক্লাসে উপস্থিতি, এবং পূর্বের পরীক্ষার ফলাফল। তুমি এই তথ্যগুলো দেখে একটা সিদ্ধান্ত নিতে চাও যে সে পাস করবে কিনা। কিন্তু এক্ষেত্রে তুমি চাও একটা নির্দিষ্ট মডেল যা প্রতিটি ফ্যাক্টরকে বিবেচনা করে সম্ভাবনা নির্ধারণ করবে।
লজিস্টিক রিগ্রেশন ঠিক এভাবেই কাজ করে। এটি বিভিন্ন ফ্যাক্টর বা ভেরিয়েবল ব্যবহার করে ভবিষ্যদ্বাণী করে—একটি বিষয় প্রাসঙ্গিক (যেমন, পাস করা) নাকি অপ্রাসঙ্গিক (যেমন, ফেল করা)।
কাজের প্রক্রিয়া:
.
1. তথ্য সংগ্রহ: লজিস্টিক রিগ্রেশন অনেকগুলো ইনপুট (ভেরিয়েবল) নিয়ে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, গুগলের ক্ষেত্রে, একটি ওয়েবসাইট প্রাসঙ্গিক কিনা তা বের করার জন্য বিভিন্ন তথ্য দেখা হয়, যেমন:
লিংকে কতজন ক্লিক করছে।
লিংকে প্রবেশের পরে তারা কতক্ষণ সেখানে থাকে।
লিংকটি কতবার শেয়ার করা হয়েছে বা রেট করা হয়েছে।
কনটেন্টে কীওয়ার্ড মিলছে কিনা।
.
2. ওজন নির্ধারণ: (Weight Fixing)
ধরে নাও, রাহাতের পড়াশোনার সময়, ক্লাসের উপস্থিতি, এবং পূর্বের পরীক্ষার ফলাফল—প্রতিটি ফ্যাক্টরই ভিন্ন ওজন (Weight) বহন করে। তার মানে, হয়তো তার পূর্বের পরীক্ষার ফলাফল পাস করার সম্ভাবনায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আর ক্লাসের উপস্থিতি একটু কম গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। লজিস্টিক রিগ্রেশন এই (Weight) বিশ্লেষণ করে।
.
3. প্রোবাবিলিটি নির্ধারণ: (Probability Calculation)
লজিস্টিক রিগ্রেশন প্রতিটি ইনপুট ফ্যাক্টর থেকে একটি নির্দিষ্ট স্কোর বা সম্ভাব্যতা বের করে। এই স্কোরটি ০ থেকে ১ এর মধ্যে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, রাহাতের পাস করার সম্ভাবনা যদি লজিস্টিক রিগ্রেশন যদি বলে যে রাহাতের পাস করার সম্ভাবনা 0.8 (৮০%), তাহলে আমরা বলতে পারি, সে পাস করার সম্ভাবনা বেশি। আবার, যদি সম্ভাবনা 0.3 (৩০%) হয়, তাহলে সে সম্ভবত ফেল করবে। এইভাবেই লজিস্টিক রিগ্রেশন প্রতিটি ফ্যাক্টর থেকে একটি প্রোবাবিলিটি বা সম্ভাবনা বের করে।
.
4. প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ: (Relevancy)
গুগলের ক্ষেত্রে, একটি লিংক প্রাসঙ্গিক কিনা তা নির্ধারণ করতে লজিস্টিক রিগ্রেশন ব্যবহার করে দেখা হয় প্রতিটি ওয়েবসাইট কতটা প্রাসঙ্গিক ফ্যাক্টর পূরণ করছে। গুগল যদি দেখে যে একটি লিংক ০.৭ (৭০%) সম্ভাবনা নিয়ে প্রাসঙ্গিক, তবে সেটি প্রাসঙ্গিক হিসেবে ধরা হয়। অন্যদিকে, ০.৩ (৩০%) সম্ভাবনায় লিংকটি হয়তো কম প্রাসঙ্গিক হতে পারে।
প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক আলাদা করার মূল কৌশল:
========================================
.
লজিস্টিক রিগ্রেশন সরাসরি “হ্যাঁ” বা “না” বলে না, এটি সম্ভাব্যতা প্রদান করে। এই সম্ভাব্যতা থেকে আমরা বুঝতে পারি, কোনো কিছু প্রাসঙ্গিক কিনা। গুগল এভাবে প্রতিটি সার্চ রেজাল্টের সম্ভাব্যতা বের করে, তারপর ০.৫ (৫০%) এর ওপরে থাকা লিংকগুলোকে প্রাসঙ্গিক এবং ০.৫ এর নিচের লিংকগুলোকে কম প্রাসঙ্গিক হিসেবে দেখায়।
.
সারসংক্ষেপ:
লজিস্টিক রিগ্রেশন প্রতিটি ফ্যাক্টরের weight বিশ্লেষণ করে একটি প্রোবাবিলিটি নির্ধারণ করে। যদি সেই প্রোবাবিলিটি ৫০% এর উপরে হয়, তাহলে সেটি প্রাসঙ্গিক হিসেবে ধরা হয়, আর নিচে হলে অপ্রাসঙ্গিক। গুগল এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সার্চ রেজাল্ট ফিল্টার করে প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক লিংকগুলো আলাদা করে।
.
.
**( এটি একটি অতি সরলভাবে ব্যাখ্যা করা বিষয়। গাণিতিক ব্যাখ্যা এর থেকে জটিল)
.
.
Please Comment: next